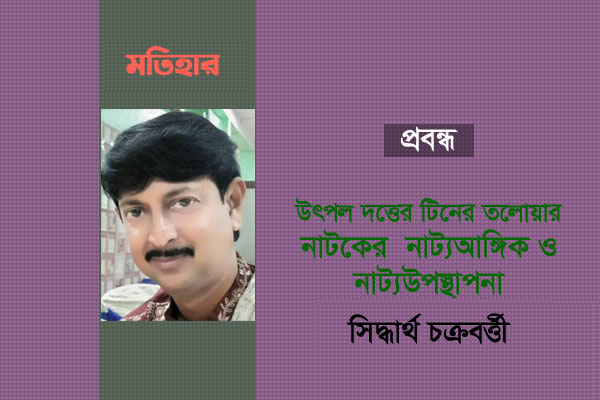যে সমস্ত শিল্পী ও স্রষ্টারা তাঁদের শিল্পের মধ্যে দিয়ে এই সমাজটাকে আরও উন্নত ও শোষণমুক্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তাঁদের শিল্পটাকেই সে কাজে হাতিয়ার বা অস্ত্র করে তুলতে, সেই ধারার একেবারে প্রথম সারিতে আমরা দেখতে পাই উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩)-কে। একইসঙ্গে অভিনেতা, নির্দেশক ও বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার। তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকেই ফুটে উঠেছে রাজনীতি, সমাজ সচেতনতা ও সমকালীন প্রেক্ষিত। আলোচ্য নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে চলত সরকারি নির্যাতন। সেই উত্তাল সময়ে এল.টি.জি. (লিটল থিয়েটার গ্রুপ) নাট্যদল ভেঙে ‘বিবেক নাট্য সমাজ’ হয়ে জন্ম নেয় পি.এল.টি (পিপলস লিটল থিয়েটার) নাট্যদল। উৎপল দত্তের হাতে তখন আর মিনার্ভা থিয়েটার হলটি নেই। তাই বিভিন্ন থিয়েটার হল ভাড়া করে। তখন তাঁকে দল চালাতে হচ্ছিল। নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭-৬৮) থেকে বেরিয়ে আসার পর সবদিক দিয়েই উৎপল দত্ত খুব একা হয়ে পড়েছিলেন। সেইসময় শতবর্ষ আগের বাংলা থিয়েটারের সংগ্রামী অতীতকে আধার করে লিখলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ‘টিনের তলোয়ার’। কাল্পনিক এক কাহিনীর আড়ালে ফুটিয়ে তুললেন সেদিনের নাট্যকর্মীদের জীবন যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র। সাল-তারিখের হিসেবকে অগ্রাহ্য করে তুলে ধরলেন তাঁদের সংগ্রামী অতীতকে। কল্লোল (১৯৬৫) নাটকের কালজয়ী জনপ্রিয়তার পর এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি তাঁকে আবারও নিয়ে যায় খ্যাতির শীর্ষে। ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে খ্যাতি অম্লান ছিল। নাট্যচর্চা ও চলচ্চিত্রাভিনয়ের পাশাপাশি ১৯৬৮ সাল থেকে উৎপল দত্ত যাত্রাপালা লিখতে ও নির্দেশনা দিতে শুরু করেন। সেই অভিজ্ঞতার আস্বাদও আমরা পাই এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে। উৎপল দত্ত তাঁর সেন্ট জেভিয়ার্সের কলেজ জীবন (১৯৪৫-৪৯ ) থেকেই ইংরেজি নাট্যচর্চার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যান। আর ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে বিখ্যাত ইংরেজ নির্দেশক ও অভিনেতা জিওফ্রে কেন্ডাল (Geoffrey Kendal, 1909-98) তাঁর নাট্যদল ‘The Shakespeareana International Theatre Company’ নিয়ে যখন কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের Garrison Theatre (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের নিজস্ব নাট্যগৃহ, যেখানে একসময় ছিল ইংরেজদের বিখ্যাত সাঁ সুসি থিয়েটার)-এ অভিনয় করতে আসেন, তখন কিশোর উৎপল সেই নাট্যদলে একজন পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে গণনাট্য সংঘ (১৯৫১-৫২)-এ থাকাকালীন তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই যখন দলের প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য হয়ে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন, তখন পাশ্চাত্য রীতির পাশাপাশি বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকেও স্মরণে রাখেন।
ঊনিশ শতকের বাংলার সমাজ ধীরে ধীরে বদলাচ্ছিল। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছাল ইউরোপীয় রেনেসাঁসজাত মুক্ত চিন্তা-ভাবনার অভিঘাত। এল যুক্তি ও মানবতাবাদ। আর সেই সঙ্গে হেনরি ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৮-১৮৭৩) প্রমুখ মনীষীদের বিবিধ সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডে বহুযুগের জমে থাকা অন্ধ কুসংস্কার, প্রাচীন ধর্মীয় গোড়ামি আর অজ্ঞ রক্ষণশীলতা ক্রমশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকলো নতুন যুগের জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে।
বাংলা থিয়েটারের শুরু থেকেই নাটককারদের মধ্যে দেখা গেছে সমাজসচেতনতা, তাঁরা তাঁদের নাটকের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তা বোধের পাশাপাশি সমাজকেও সংস্কার করতে চেয়েছেন নানান কু-সংস্কার ও কু-প্রথা থেকে। তুলে ধরেছেন পরাধীন স্বদেশবাসীর অসহায় জীবন যন্ত্রণার ছবি। যা এতই গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, ইংরেজ শাসককেও ভয়ে কম্পিত হতে হয়েছে বারংবার। নাটকের টিনের তলোয়ারের ঝনঝনানিকে ভয় পেয়েই তারা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রন আইন। একের পর এক নাটকের অভিনয় বন্ধ করে, নিষিদ্ধ করে, নাট্যপুস্তক বাজেয়াপ্ত করে তারা থামিয়ে রাখতে চাইছিল এ দেশের সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে। উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন যে, “এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যত সমাজের ভ্রূণ। একদল মানুষ এই সমাজব্যবস্থাকেই চরম ও পরম বলে স্বীকার করেন না ; তাঁরা ঐ ভ্রূণাবস্থায় থাকা ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ রূপ মনশ্চক্ষুতে দেখতে পান এবং সেই সমাজের কথা বলেন। তবে অবশ্যই তাঁরা সংখ্যায় অত্যল্প এবং প্রতি মুহূর্তে নির্যাতিত। তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য শাসকদের বিপুল প্রচার ছাড়াও নিত্যনতুন আইন রচিত হয় যাতে তাঁদের গান কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে গিয়ে গাইতে হয়। ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রন আইন এই রকমই একটা অস্ত্র।১ উৎপল দত্ত তাঁর এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকটি লিখেছিলেন শতবর্ষ আগের বাংলা থিয়েটারের সেই ব্যতিক্রমী মানুষদের প্রণাম জানাতে। যাঁরা সেদিনের কুষ্ঠগ্রস্থ সমাজের নিয়ম নীতিকে অস্বীকার করে, শাসকপক্ষের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে নাটককে বিপ্লব ও বিদ্রোহের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের নাট্যরীতি প্রচলিত নাট্যরীতির থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এটি একটি ব্যতিক্রমী বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নাটক।
এই ‘টিনের তলোয়ার‘ নাটকে রয়েছে সাতটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখি মধ্যরাত্রে কলকাতার রাস্তায় দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার নতুন নাটক ‘ময়ূরবাহন‘-এর পোস্টার সাঁটা হচ্ছে। বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবু নটবরকে আরও কয়েকটা জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেন। ম্যানহোল দিয়ে নীচে নেমে মাটির তলার নর্দমা পরিস্কারের কাজ করছিলেন মথুর নামে এক মেথর, বেণীমাধব মদের ঘোরে তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি থিয়েটার দেখেন? মেথর জবাব দেন ‘না’। তারপর মেথর বেণীমাধবকে বলেন, এত নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষি কর কেন?……… যা আছো তাই সাজো না।………কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে নাটক লিখতে পারবে?’ এই সময় ময়নার ডি-শাপে গাওয়া গান বেণীমাধবের কানে আসে। তিনি গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মেথরকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাংলার প্রখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নক্সা নাটক ‘থিয়েটার” থেকে নেওয়া ‘ছেড়ে কলকেতা বন– হব পগার পার’ গানটি দিয়ে প্রথম দৃশ্যটি শেষ হয়। এই দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে নাটককার উৎপল দত্ত এ নাটকের মুখবন্ধটি তৈরি করে দেন। শতবর্ষ পূর্বের বাংলা থিয়েটারের সামগ্রিক অবস্থার কিছুটার পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই এই প্রথম দৃশ্যটি থেকে। এমনকি সেই সময়ের প্রচলিত থিয়েটারের সঙ্গে যে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের সেভাবে কোনও যোগসূত্র ছিল না সেটাও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রথম দৃশ্যটির মধ্যে দিয়ে আলোচ্য ঘটনাবলি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল তৈরি হয়। এই অংশটিকে আমরা প্রস্তাবনা বা Exposition বলতে পারি। যদিও বহু নাটকের মতন এ নাটকটিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনও নাট্যতত্ত্বের বিধিকে হুবহু মেনে লেখা হয় নি। সাধারণত যখন নাটককার কোনও নাটক লেখেন তখন তিনি সেই নাটকের মূল ঘটনা ও চরিত্রদের বিকাশকেই প্রাধান্য দেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর নাট্যরচনার গতি-প্রকৃতির কিছুটা হয়ত নাট্যতাত্ত্বিকদের ভাবনার সঙ্গে মেলে, আর কিছুটা সেই নাটককারের নিজস্বতা হয়ে রয়ে যায়।
এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এই দৃশ্যেই আমরা একইসঙ্গে Plot বা বৃত্তের অগ্রগতি ও তার জটিলতা প্রাপ্তির ঘটনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হই। এই দৃশ্যের পটভূমি চিৎপুরে বেঙ্গল অপেরার মহলাকক্ষ। নাট্যদলের অভিনেতারা নিজেদের পার্ট মুখস্থ করছেন, তৎকালীন ভারত সংস্কারক পত্রিকায় বেঙ্গল অপেরার সধবার একাদশী’ নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বারাঙ্গনা পল্লীর নারীদের নিয়ে থিয়েটার করায় নিন্দা করেছেন। এ নাটকের ‘যদু’ চরিত্রটি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের “থিয়েটার’ নামের নক্সা নাটক থেকে গৃহিত ও লো রাঙ্গা বৌ, তোরা কেউ কাগজ পড়িস লো’ গানটি গেয়ে ওঠে। পাড়ার মুদি ধার না শোধবার কারণে মহলা কক্ষে এসে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির শিষ্যা বিখ্যাত অভিনেত্রী আঙুর ওরফে বসুন্ধরা দেবীকে বেশ্যা বলে অপমান করে চলে যায়। সমসাময়িক থিয়েটারের কথাও জানতে পারা যায় এই দৃশ্যে। এই সময় নোংরা শাড়ি পরে আলু- বেগুন বেচনেওয়ালি ময়না মহলা কক্ষে প্রবেশ করে কান্তেনবাবুর খোঁজ করেন। দলের লোকজন তাকে ছদ্মবেশী নারী দস্যু বা পুলিশের চর বলে সন্দেহ করে। এমনকি পুলিশের বড়কর্তা (ডেপুটি কমিশনার) ছদ্মবেশী ল্যামবার্ট সাহেব বলেও ভেবে ফেলেন। বেণীমাধব ঘুম ভেঙে উঠে ময়নাকে চিনতে পারেন। পেয়ারাকে বলেন ময়নাকে ভালো করে স্নান করিয়ে পরিস্কার করে, রাজকুমারী অনুরাধার বেশ ও অলংকার পরিয়ে নিয়ে আসতে। ময়না লজ্জা পেলে বেণীমাধব বলেন রাগ, লজ্জা, ভয় এই তিন থাকলে থিয়েটারে স্থান নেই। হরবল্লভ কাল্ডেনবাবুকে বলেন অনুরাধার পার্টটা বেশ শক্ত, কারণ নাটকটা শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট আর ম্যাকবেথ মিশিয়ে মেরে দেওয়া। ওফিলিয়াই হচ্ছে অনুরাধা। প্রত্যুত্তরে বেণীমাধব বলে ওঠেন –
“বেণী ॥ (অধৈর্য স্বরে) শিখিয়ে নেব। বেণীমাধব চাটুয্যে বলছে, শিখিয়ে নেবে। বেণীমাধব চাটুয্যে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কাঠ পুগুলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে। এখানে কে অভিনয় করতে পারে? একজন ছাড়া- ঐ আঙুর, সে করে অভিনয়। আমরা জলে আঁক কাটি। এই যে বেণীমাধব চাটুয্যে ছোট বেলা থেকে যাত্রায় গাইছি। বিশ বছর একাদিক্রমে অভিনয় করে বুঝলাম আমি অভিনয় করতে জানি না।
প্রিয় ॥ (হঠাৎ) তখন অভিনয় ছেড়ে দিলেন না কেন?
বেণী ॥ ততক্ষণে আমি বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছি যে। (সকলের মৃদু হাসি) কিন্তু আমি শিক্ষক। আমি স্রষ্টা। আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জীবন্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান। আমি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।”
এই সময়ে মহলা কক্ষের জানলার কাঁচ ভেঙে বেণীমাধবের পিঠে ইট এসে লাগে। সেই সঙ্গে বাইরে থেকে নানা আপত্তিকর মন্তব্যও ভেসে আসে। দলের লোকেরা ঢাল বার করে আত্মরক্ষা করে। প্রিয়নাথ উত্তেজিত হয়ে হাতাহাতি করতে চাইলে বেণীমাধব বলেন তাতে লাভ হয় না, পুলিশ নাট্যদলের লোকেদেরকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। সেকালের থিয়েটারকে যে সে সময় সমাজের নানা স্তরের প্রতিবন্ধকতা কে পেরিয়ে কাজ করতে হয়েছিল এ থেকে তা বুঝতে পারি আমরা। প্রিয়নাথের পরিচয় প্রকাশিত হয়। তিনি হিন্দু কলেজের ক্যাপ্টেন পেণ্ডেলবেরির কাছে নাটক শিখেছেন, এবং পার্ক স্ট্রীটের সাঁ সুসি থিয়েটারে ইংরেজিতে অভিনয় করেছেন। তিনি তিন বছর ধরে পরিশ্রম করে ব্রিটিশ দস্যু জালিয়াত ক্লাইভের মুখোশ উন্মোচন করে পলাশীর যুদ্ধ’ নামে একটি নাটক লিখে, সেটি পড়তে দিয়ে গেছিলেন বেণীমাধবকে, কিন্তু সে নাটক পড়া হয়নি। নাটকের পৃষ্ঠাগুলোকে ঠোঙা বানিয়ে দলের ঘরে মুড়ি খাওয়া হয়েছে। প্রিয়নাথ এই ঘটনায় অত্যন্ত হতাশ হয়ে বলেন,
প্রিয় । (ভগ্ন স্বরে) ভেবেছিলাম আপনাদের রিফরমেশনের আলোকে টেনে আনবো। ভেবেছিলাম ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা দেব। (সজোরে) এবং আমিই পারবো। মাইকেল চলে গেছেন, দীনবন্ধু গত হয়েছেন।
বেণীমাধব তাঁর এই সব কথা শুনে রেগে যান। যদু এই শ্রেণীর বাবুদের ব্যাঙ্গ করে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের “মজা’ নক্সা নাটকের গান গেয়ে ওঠেন- সাচ্চা বুলি আমরা বলি, ভয় করি না তাই’। পুনরায় ইঁট পাটকেল আসতে থাকে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বাচস্পতি লাঠিয়াল নিয়ে মহলা কক্ষে এসে এ পাড়া থেকে নাট্যদলকে উঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলে প্রিয়নাথ রুখে দাঁড়ায়। তাঁর মুখে চোস্ত ইংরেজি শুনে বাচস্পতি ও তার দলবল ঘাবরে গিয়ে পলায়ন করে। বেণীমাধব প্রিয়নাথকে পরামর্শ দেয় বাংলা নাটক লিখতে হলে থিয়েটার কাকে বলে, কী ভাবে তা হয় সেটা সম্যকভাবে জানতে হবে। প্রিয়নাথ সেটা মেনে নেয়, তবে তিনি বেণীমাধবকে মদ্যপান করে স্টেজে না নামতে পরামর্শ দেন। এই সময় দলের স্বত্বাধিকারী, সাহেবের মুৎসুদ্ধি বীরকৃষ্ণ দাঁ দু-জন চাপরাশি নিয়ে প্রবেশ করেন। বেঙ্গল অপেরার অভিনেত্রী মানদা সুন্দরীকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভুবন মোহন নিয়োগী নিয়ে গেছেন শুনে হতাশ হন। বলেন যে দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত এঁরা মোটেই নাটক লিখতে পারেন না। এরপর থেকে তিনি বরং কাউকে ভাড়া করে রেখে নাটক লিখবেন। বেণীমাধব ময়নাকে ভদ্র ঘরের মেয়ে শঙ্করী সাজিয়ে নতুন নাটকের নায়িকা হিসেবে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। বীরকৃষ্ণ তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিশ্চিন্তে চলে যান। বেণীমাধব কঠোর পরিশ্রমে অশিক্ষিত ময়নাকে অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে থাকেন। সেকালের থিয়েটারকে যে কতরকমের বাঁধার সম্মুখীন হতে হত প্রতি পদে পদে, খুব নিপুণ ভাবে তার পরিচয় নাটককার এই দৃশ্যে আমাদের জানিয়ে দেন। এই দৃশ্যটিকে আমরা প্রথম দৃশ্যের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখতে পাই। যেখানে নাট্যঘটনা ক্রমশ বিস্তৃত ও জটিল হয়ে উঠছে এবং নাট্যঘটনার অগ্রগতিতে নানা বৈচিত্রপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।
তৃতীয় দৃশ্য শুরু হচ্ছে দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার শোভাবাজারস্থ রঙ্গমঞ্চে, যেখানে মঞ্চ ও নেপথ্য ভূমি দুই-ই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শুরু হতে চলেছে ‘ময়ূরবাহন’ নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। অভিনেতারা নিজ নিজ পার্ট নিয়ে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। দলের বাকি অভিনেতারা নবাগতা ময়নাকে আশীর্বাদ করে ভরসা দেয়। বেনীমাধব ময়ূরবাহনের মতন একটা ওঁচা নাটক ধরেছেন বলে আপশোস করেন। ভদ্র ঘরের মহিলা মঞ্চে এই প্রথম নামছে প্রচারে হল ভর্তি হয়ে যায়। বীরকৃষ্ণ দাঁ এসে জানান যে শহরের গণ্যমান্য মানুষে হল বোঝাই। বর্ধমানের রাজা, ভূকৈলাশের রাজা আর পণ্ডিত কিশোরীলাল তর্কপঞ্চানন সামনের সারিতে উপবিষ্ট। তার মান যেন বজায় থাকে, তা নইলে কাপ্তেনবাবুকে তিনি আর দলে রাখবেন না। নাটক শুরু হয়, ময়নার গান ও অভিনয় দেখে দর্শকেরা উচ্ছসিত হয়। তারা বারংবার ময়নাকে দেখতে চায়। বীরকৃষ্ণ দাঁ এসে কাপ্তেনবাবুকে বলেন যে লোকে শঙ্করীকে দেখতে চাইছে, তার একটা নাচ-টাচ লাগাতে। বেণীমাধব তাকে হাটিয়ে দিয়ে বলেন সে এখন শঙ্করী নয়, অনুরাধা। নাটক জমে উঠলেও কিছু দর্শকের কোলাহলে বিক্রম বেশী বেণীমাধব অভিনয় থামিয়ে সেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন- ‘মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেথায় স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন। এটা নাট্যমন্দির। জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেরিয়ে যান।’ নাটকাভিনয় আবার শুরু হয়। বিক্রম বেশী বেণীমাধব ও সাবিত্রী রূপী বসুন্ধরার অভিনয়ে নাটক যখন তুঙ্গে তখন হঠাৎ মঞ্চে অনুরাধা রূপী শঙ্করী ওরফে ময়নার হাত ধরে উপস্থিত হন বীরকৃষ্ণ। প্রেক্ষাগৃহে করতালির ঝড় ওঠে। ময়না হাত জোর করে বাবুদের নমস্কার করেন। তৃতীয় দৃশ্য এখানেই শেষ হয়। বোঝাই যায় তৎকালীন যুগে থিয়েটার মালিকের এই রকম নানা অসভ্যতামিকে সহ্য করতে বাধ্য হত থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। দলের শেষ কথা বলত এই মালিক পক্ষ। যারা অর্থ, মদ ও মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। বেণীমাধবের মতন মানুষেরা যাঁরা থিয়েটার ছাড়া কিছুই বুঝতে চাইতেন না তাঁদের মনের মধ্যে অসম্মানের আগুন জ্বলতে থাকে। নাট্য ঘটনার উর্ধগতি এই দৃশ্যে সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়। ইংরেজিতে আমরা একে rising action বলতে পারি।
চতুর্থ দৃশ্যে দেখতে পাই ময়না বৌবাজারের রাস্তায় সাজ-সজ্জা করে ঘুরতে বেরিয়েছে। পূর্ব পরিচিত মেথর মথুর তাকে দেখে বলে ‘তুমি তো মুচির কুকুরের মতন ফুলে উঠেছ দেখছি।’ ময়না তাকে তার নতুন জীবনের নানা গল্প শোনায়, তারপর বলে ‘চলি, এখানে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা কওয়াটা তেমন ভালো দেখায় না। মথুর, জীবন থেকে কিছুই পেলি না রে।’ দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মানুষ ময়নার কাছে ভিক্ষা চাইতে এলে ময়না তাদের ভিক্ষা না দিয়ে সরে যায়। এক ক্রুদ্ধ যুবক বাবুদের বিদ্রুপ করে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা নাটক থেকে গান ধরেন— ‘দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।’ ইউরোপীয় পোষাক পরে ছড়ি হাতে প্রিয়নাথ আসে ময়নার কাছে। ভিক্ষুককে প্রিয়নাথ পয়সা দেয়। ময়না ওদের সহ্য করতে পারে না। বলে – আমিও ওমনি করেই কলকাতায় এসেছিলাম। – বহুদিন আগে।’ আজ ময়না তার সেই ক্লেদাক্ত অতীতটাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে চায়। পূর্বোক্ত যুবকটি আবার এসে দাঙ্গার খবর জানায় প্রিয়নাথকে। ইন্দ্র সাহার চালের আড়াতে ভিখিরির দল পেটের জ্বালায় খাবলা মারায় পুলিশ সাহেব ল্যাম্বো এসে পেটাচ্ছে ভিখিরিদের। প্রিয়নাথ ক্ষোভে ফেটে পড়েন, সে ময়নাকে বোঝায় কেন এই দুর্ভিক্ষ তৈরি হয়েছে। ময়না বাবু বাড়ির বুলবুলির লড়াই দেখবার জন্য উদগ্রীব। এ সবে তার মন নেই। এর মধ্যে গভর্নর বাহাদুরের লোক এসে জানিয়ে যায়— কোনো রকম অস্ত্র রাখলে ভারতীয়দের কয়েদখানায় আটকে রাখা হবে। বাচস্পতি তার লোকজন নিয়ে এসে ময়না ও প্রিয়নাথকে টিটকিরি ও অপমান করে চলে যায়। এমনকি প্রিয়নাথের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রিয়নাথ সহুংকারে ছড়ি চালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এই দৃশ্যে আমরা ময়না ও প্রিয়নাথের মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে দেখতে পাই। সেই সঙ্গে জানতে পারি ইংরেজদের শোষণে দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা। এই দৃশ্যটি নাট্য কাহিনীর উর্ধগতিকে ত্বরান্বিত করেছে।
পঞ্চম দৃশ্যে দেখি নাটকের গতি আরও তীব্র হয়েছে। এই দৃশ্যটির পটভূমি বেঙ্গল অপেরার থিয়েটার গৃহে বেণীমাধবের সাজঘর। ‘সধবার একাদশী’ নাটকের শেষে সেখানে প্রিয়নাথ ও বেণীমাধব আলোচনায় রত। প্রিয়নাথ জানায় গ্রেট ন্যাশনাল এবার উকিল জগদানন্দকে ব্যঙ্গ করে ‘গজদানন্দ’ নাটক ধরেছে। যার গান গুলি লিখেছেন স্বয়ং গিরিশ্চন্দ্র। বেণীমাধব বলেন ওই প্রহসনটির বিক্রী কোনোভাবেই তাদের দলের থেকে বেশী হবে না। প্রিয়নাথ তাঁর কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, এই নাটক অভিনয় করে গ্রেট ন্যাশনাল ব্রিটিশ শাসক ও তার নেটিভ মোসাহেবদের মুখে জুতো মারছে সেটা কি তিনি বুঝছেন না। বেণীমাধব তখন তাকে বেঙ্গল অপেরা যে একটানা তিন মাস হাউসফুল যাচ্ছে সে খবর দেন অতি উৎসাহের সঙ্গে। প্রিয়নাথ তাঁকে দেশের নিদারুন অবস্থার কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। এই ঘরেই সকলের অলক্ষ্যে মালিক বীরকৃষ্ণ বসেছিলেন এতক্ষণ, আধো- অন্ধকার থেকে তিনি আলোয় বেরিয়ে আসেন। তিনি জানান সম্প্রতি ব্যবসায় তার সাড়ে তিন লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। তাই তিনি এ থিয়েটার তুলে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। বেণীমাধব কাতরভাবে তাকে বলেন এতগুলো মানুষ তাহলে না খেতে পেয়ে পথে বসবে। বীরকৃষ্ণ তখন প্রস্তাব দেন তিনি তার শ্যামবাজারের জমি ও সেইসঙ্গে থিয়েটার গৃহ তৈরি করার জন্য আট হাজার টাকা দেবেন। এমনকি তিনি আর থিয়েটার ব্যবসায় থাকবেন না, স্বত্তাধিকারী করে দেবেন বেণীমাধবকেই, উকিলের থেকে তিনি দলিল করে এনেছেন। বেণীমাধব এ কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হলে প্রিয়নাথ প্রিয়নাথ তাঁকে বলেন – বীরকৃষ্ণ প্রতিদানে কী চান সেটা জেনে নিতে। বীরকৃষ্ণ জানান প্রতিদানে তিনি ময়না ওরফে শঙ্করীকে তার রক্ষিতা করে রাখবেন। এই প্রস্তাবে প্রিয়নাথ শিহরিত হলেও বেণীমাধব সম্মতি জানান। নিজেদের থিয়েটার হবে এ কথা শুনে বসুন্ধরা ও ময়নাও আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। কারণ বসুন্ধরা আর বেণীমাধব চার বছর আগে থেকেই নিজেদের থিয়েটার বাড়ি তৈরি করবার নক্সা তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। প্রিয়নাথ তাদের থামিয়ে বলেন, ‘কালনেমির লঙ্কাভাগটা পরে করবেন। আগে জিজ্ঞেস করুন কি মূল্যে বেণী বাবু থিয়েটার কিনছেন?” বেণীমাধব নির্বিকার ভাবে জানায় ময়না বীরকেষ্টর ধোপাপুকুরের বাড়িতে থাকবে। বীরকেষ্ট তাকে বাড়ি দেবে, গয়না দেবে, পাটরানি করে রাখবে। কারণ ও ছিল রাস্তার ভিখিরি, যা এখন পাচ্ছে বর্তে যাবে। ময়না এ কথা শুনে প্রতিবাদ করে জানায়, ‘ভিখিরি যখন ছিলাম, তখন তরকারি বেচে পেট চালাতাম। এখন এমন ভদ্রমহিলা বানিয়েছো বাবু, যে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর পথ নেই।” প্রিয়নাথ বেণীমাধবকে তিরস্কার করে বলেন যে তার কোনও মরালিটি, নীতিবোধ, ন্যায়বোধ নেই। বেণীমাধব বলেন, ‘নীতিবোধ নিয়ে চললে আর থিয়েটার করতে হত না এ দেশে। বীরকৃষ্ণ দায়েদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে থিয়েটার চালাতে হয়। তাই চালিয়ে আসছি বহু বৎসর। গলায় নীতির পৈতে ঝুলিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী সাজলে এই কলকাতায় না হত থিয়েটার, না হত নাচ-গান, না হত নাটক-নভেল লেখা।’ বসুন্ধরা এভাবে ময়নার সতীত্ব বিক্রি করে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান না। তিনি প্রিয়নাথকে বলেন ময়নাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে, নতুন সংসার বাঁধতে। কিন্তু ময়না জানায় থিয়েটার ছাড়া সে বাঁচবে না, এরাই তার পিতা মাতা, ভাই বোন। এদেরকে পথে বসিয়ে সে চলে যেতে পারবে না। আবার দারিদ্রের মধ্যেও সে আর থাকতে পারবে না। বসুন্ধরা তাঁর নিজের ঘর বাঁধবার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ময়নার জীবনের পূর্ণ হোক সেটা চেয়েছিলেন। কিন্তু ময়না থিয়েটারের প্রতি গভীর ভালোবাসায় বীরকৃষ্ণের দেওয়া গয়না পড়ে নেয়। নাট্যতত্ত্ব অনুযায়ী এই দৃশ্যটিকে বৃত্তের অবরোহ বা falling action বলতে পারি আমরা,এছাড়াও এই দৃশ্যটিকে নাটকের turning point হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি।
ষষ্ঠ দৃশ্যে আমরা দেখি প্রিয়নাথের লেখা ব্রিটিশ বিরোধী নাটক ‘তিতুমীর’-এর মহলা চলছে। বেণীমাধব তিতুমীরের সংলাপ বলছে এবং অন্যদের সংলাপ কীভাবে বলতে হবে সেটা শিখিয়ে দিচ্ছেন। যদিও প্রিয়নাথ আর মহলায় আসছেন না। বেণীমাধব স্বীকার করেন প্রিয়নাথ নাটক ভালোই লেখেন। অনেক রাত করে প্রচুর গয়না পড়ে মিষ্টি নিয়ে ময়না বীরকৃষ্ণের সঙ্গে প্রবেশ করেন মহলা কক্ষে, কারণ কত্তার বড় ছেলের জন্মদিন ছিল আজ। আবার মহলা শুরু হলে ময়না বঙ্গলক্ষ্মীর ‘স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির্মণ্ডলী’ (এই গানটি ডিরোজিওর লেখা ইংরেজি কবিতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ থেকে ঈষৎ পরিবর্তন করে গ্রহণ করা হয়েছে) দেশপ্রীতিমূলক এই গানটি গাইতে শুরু করলে বীরকৃষ্ণ আপত্তি জানিয়ে বলেন, ‘এই তিতুমীর নাটকটি হতে পারছে না, কারণ এ নাটক সাহেবদের গাল দিচ্ছে। এছাড়া তিনি জানান যে, সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গীতিনাট্য ‘সতী কি কলঙ্কিনী-র অভিনয় চলাকালীন পুলিশ এসে অশ্লীলতা ও রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেন। তার মধ্যে ছিলেন নাট্যকার ও নির্দেশক উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু), মতিলাল সুর, সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যাল প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সত্যি এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ। উৎপল দত্ত সুকৌশলে সেই ঐতিহাসিক তথ্য এই নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ময়না কাপ্তেনবাবুকে বলেন, ‘কই কাপ্তেনবাবু, বলে দাও ওকে – ‘ঢেউ দেখেই নাও – ডোবাবার লোক তুমি নও। বলে দাও প্রিয়নাথের নাটক তুমি করবেই। সাহেব আর পুলিশকে ডরাবার পাত্র তুমি নও।’ বেণীমাধব ‘তিতুমীর’ বন্ধ রেখে ‘সধবার একাদশী’ করবেন বলে স্থির করেন। ময়না বেণীমাধবের এ সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানিয়ে তাঁকে অপমান করে দল ছেড়ে চলে যান। কারণ সে চেয়েছিল তার মনের মানুষ প্রিয়নাথ মল্লিক (যে চরিত্রের মধ্যে কিছুটা উপেন্দ্রনাথ দাসের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়)-এর লেখা বিদ্রোহী নাটক ‘তিতুমীর’ মঞ্চস্থ করুন কাপ্তেনবাবু, কারণ প্রিয়নাথের নাম করলেই বীরকৃষ্ণ তাঁকে মারে। তাই সে আরও বেশী করে প্রিয়নাথের কথা বলে। বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবু সকলের অবর্তমানে বসুন্ধরাকে বোঝান থিয়েটার দল চালাতে গেলে হঠকারিতা চলে না, তিনি বলেন, ‘আমার একটা দায়িত্ব নেই? দলের লোকগুলোর রুজি রোজগারের দায়িত্বটা আমার নয়? আমি জেলে গিয়ে বসে থাকলে এদের কি হবে? থেটার উঠে গেলে দেশের খুব উপকার হবে? দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? ইংরেজ পালাবে? কি যে সব বলে!’ বেণীমাধব চরিত্রটি এ নাটকের Protagonist চরিত্র, তাঁর মধ্যে সেকালের বহু অভিনেতা ও নির্দেশকের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে এই চরিত্রের সাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। নিজেদের থিয়েটার হল পাওয়ার জন্য তিনিও বিনোদিনীর মতন ময়না কে বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হয়ে থাকতে প্ররোচিত করেন। তবে তিনি যা কিছু করেন সবই থিয়েটারকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকিয়ে রাখার জন্য। তাই এই দৃশ্যে দেখি, দলের সকলের চোখে ছোট হয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আসলে আমি বড় একা। কেউই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা। সেকালে যাঁরা থিয়েটার চালাতেন তাঁদের অনেক কিছুর সঙ্গেই আপসরফা করেই থিয়েটার চালাতে হয়েছিল। এই দৃশ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াতে দেখি নিঃসঙ্গ বেণীমাধবকে। নাট্যকাহিনী এখানে চরম পরিণতির শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছায়, তাই আমরা দৃশ্যটিকে Climax বলে চিহ্নিত করতে পারি।
সপ্তম তথা নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি বেঙ্গল অপেরার রঙ্গমঞ্চে ভরা দর্শকের সামনে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। দুটো বক্সে একটিতে বীরকৃষ্ণ দাঁ, ময়না ও পরিচারকগণকে দেখা যাচ্ছে, আর অন্যটিতে ব্রিটিশ পুলিশের বড়কর্তা ল্যামবার্ট ও অন্যান্য ইংরেজ রাজপুরুষেরা রয়েছেন। বেণীমাধব অত্যাধিক মদ্যপান করে নিমচাদের সংলাপ বলছেন, যদিও মাঝে মধ্যে সেই সংলাপের বাইরে বেরিয়ে তিনি বীরকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রোধ এবং হতাশা প্রকাশ করছেন। সেই হতাশা ও কষ্ট থেকেই বেণীমাধব বলে ওঠেন, ‘উঠোনে নাচবার বায়না নিয়েছি। ঐ সব এঁড়ের দল কড়ি ফেলে আমাদের নাচঘরে নিয়ে গেছে। তাঁর এইরূপ আচরণে সাহেবরা হেসে উঠলে বেণীমাধবের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাই তিনি হঠাৎ করে প্রিয়নাথের লেখা ‘তিতুমীর’ নাটকের সংলাপ বলে ওঠেন, ‘যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততদিন কারোর নেই বিশ্রাম। ‘নিমচাদ থেকে মুহুর্তের মধ্যে তিতুমীর হয়ে ওঠেন তিনি। কারণ তাঁর বুকের মধ্যেও জ্বলছিল দেশপ্রেমের আগুন। যে আগুন তাঁর মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন প্রিয়নাথ মল্লিক। তাঁর নাটকের চোখা চোখা সংলাপ বেণীমাধবের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই পুলিশকর্তা ল্যামবার্টের সামনে মোক্ষম সময়ে তা লাভার মত উদগীরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। নিমচাদের পোষাক পাল্টে নিয়ে তিনি পরিবর্তিত হন প্রতিবাদী কৃষক তিতুমীরে। উন্মুক্ত টিনের তলোয়ার হাতে নিয়ে সাহেব দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন ‘তিতুমীর’ নাটকের সংলাপ, ‘সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষেতি করি নি। আমরা তো ছিলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি করো, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এ দেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়ায় মাড়গে (য়ো) দিলে মোদের স্বাধীনতা?” মঞ্চের নেপথ্যে সাজ সাজ রব ওঠে। দৃশ্যসজ্জা ‘সধবার একাদশী’ থেকে বদলে ‘তিতুমীর’-এ বদলে যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে নাটকের মহলা বেণীমাধবের এ সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানিয়ে তাঁকে অপমান করে দল ছেড়ে চলে যান। কারণ সে চেয়েছিল তার মনের মানুষ প্রিয়নাথ মল্লিক (যে চরিত্রের মধ্যে কিছুটা উপেন্দ্রনাথ দাসের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়)-এর লেখা বিদ্রোহী নাটক ‘তিতুমীর’ মঞ্চস্থ করুন কাপ্তেনবাবু, কারণ প্রিয়নাথের নাম করলেই বীরকৃষ্ণ তাঁকে মারে। তাই সে আরও বেশী করে প্রিয়নাথের কথা বলে। বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবু সকলের অবর্তমানে বসুন্ধরাকে বোঝান থিয়েটার দল চালাতে গেলে হঠকারিতা চলে না, তিনি বলেন, ‘আমার একটা দায়িত্ব নেই? দলের লোকগুলোর রুজি রোজগারের দায়িত্বটা আমার নয়? আমি জেলে গিয়ে বসে থাকলে এদের কি হবে? থেটার উঠে গেলে দেশের খুব উপকার হবে? দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? ইংরেজ পালাবে? কি যে সব বলে!’ বেণীমাধব চরিত্রটি এ নাটকের Protagonist চরিত্র, তাঁর মধ্যে সেকালের বহু অভিনেতা ও নির্দেশকের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে এই চরিত্রের সাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। নিজেদের থিয়েটার হল পাওয়ার জন্য তিনিও বিনোদিনীর মতন ময়না কে বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হয়ে থাকতে প্ররোচিত করেন। তবে তিনি যা কিছু করেন সবই থিয়েটারকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকিয়ে রাখার জন্য। তাই এই দৃশ্যে দেখি, দলের সকলের চোখে ছোট হয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আসলে আমি বড় একা। কেউই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা। সেকালে যাঁরা থিয়েটার চালাতেন তাঁদের অনেক কিছুর সঙ্গেই আপসরফা করেই থিয়েটার চালাতে হয়েছিল। এই দৃশ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াতে দেখি নিঃসঙ্গ বেণীমাধবকে। নাট্যকাহিনী এখানে চরম পরিণতির শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছায়, তাই আমরা দৃশ্যটিকে Climax বলে চিহ্নিত করতে পারি।
সপ্তম তথা নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি বেঙ্গল অপেরার রঙ্গমঞ্চে ভরা দর্শকের সামনে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। দুটো বক্সে একটিতে বীরকৃষ্ণ দাঁ, ময়না ও পরিচারকগণকে দেখা যাচ্ছে, আর অন্যটিতে ব্রিটিশ পুলিশের বড়কর্তা ল্যামবার্ট ও অন্যান্য ইংরেজ রাজপুরুষেরা রয়েছেন। বেণীমাধব অত্যাধিক মদ্যপান করে নিমচাদের সংলাপ বলছেন, যদিও মাঝে মধ্যে সেই সংলাপের বাইরে বেরিয়ে তিনি বীরকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রোধ এবং হতাশা প্রকাশ করছেন। সেই হতাশা ও কষ্ট থেকেই বেণীমাধব বলে ওঠেন, ‘উঠোনে নাচবার বায়না নিয়েছি। ঐ সব এঁড়ের দল কড়ি ফেলে আমাদের নাচঘরে নিয়ে গেছে। তাঁর এইরূপ আচরণে সাহেবরা হেসে উঠলে বেণীমাধবের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাই তিনি হঠাৎ করে প্রিয়নাথের লেখা ‘তিতুমীর’ নাটকের সংলাপ বলে ওঠেন, ‘যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততদিন কারোর নেই বিশ্রাম। ‘নিমচাদ থেকে মুহুর্তের মধ্যে তিতুমীর হয়ে ওঠেন তিনি। কারণ তাঁর বুকের মধ্যেও জ্বলছিল দেশপ্রেমের আগুন। যে আগুন তাঁর মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন প্রিয়নাথ মল্লিক। তাঁর নাটকের চোখা চোখা সংলাপ বেণীমাধবের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই পুলিশকর্তা ল্যামবার্টের সামনে মোক্ষম সময়ে তা লাভার মত উদগীরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। নিমচাদের পোষাক পাল্টে নিয়ে তিনি পরিবর্তিত হন প্রতিবাদী কৃষক তিতুমীরে। উন্মুক্ত টিনের তলোয়ার হাতে নিয়ে সাহেব দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন ‘তিতুমীর’ নাটকের সংলাপ, ‘সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলে কেনে? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষেতি করি নি। আমরা তো ছিলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি করো, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার কোশ দূরে এ দেশে এসে কেনে ঐ বুট জোড়ায় মাড়গে (য়ো) দিলে মোদের স্বাধীনতা?” মঞ্চের নেপথ্যে সাজ সাজ রব ওঠে। দৃশ্যসজ্জা ‘সধবার একাদশী’ থেকে বদলে ‘তিতুমীর’-এ বদলে যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে নাটকের মহলা নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়েছিলেন। বসুন্ধরা ‘সধবার একাদশী’র কাঞ্চন থেকে ‘তিতুমীর’-এর ফতেমা সেজে মঞ্চে প্রবেশ করে বলেন, ‘কেন এয়েছে জানো না তিতুমীর? এরা হার্মাদ। জলদস্যু। এয়েছে লুট করতে। নারীর সতীত্ব নাশ করো, সোনার ভারতেরে ছারখার করে চলে যাবে সপ্তডিঙা ভাস্যে।’ করতালি ও জয়ধ্বনিতে সমগ্র হল ফেটে পরে। কামিনী গান ধরে ‘স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির্মন্ডলী’, ময়না বকস্ থেকেই সে গানের বাকিটা গেয়ে ওঠেন। পুলিশ কর্তা ল্যামবার্ট আপত্তি জানিয়ে বলে ওঠেন, ‘স্টপ দিস’। তিতুমীর বেশী বেণীমাধব বলে ওঠেন, ‘যতক্ষণ এক ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাড়গে (য়ো) থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে না কখনো।’ লেফটেন্যান্ট মাওয়ার বেশী জলদের উদ্দেশ্যে তিতুমীর বেশী বেণীমাধব বলেন- ‘ মাগুয়ার। তোমারেই খুঁজে ফিরি বারাসাতে নারকেলবেড়িয়ায়। যত নারীর সর্বনাশ করেছো, যত চাষীদের চাবুক মেরে হত্যা করেছো, সকলের প্রতিশোধ আজ আমার এই বাহুতে এসে জমা হয়েছে। দর্শক আসন থেকে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যামবার্ট ভয় দেখিয়ে বলেন- ‘ইউ উইল পে ফর দিস! আই সোয়ার ইউ উইল পে ফর দিস !’ বেণীমাধব ল্যামবার্টের শাসানিকে উপেক্ষা করে তলোয়ার চালিয়ে মাগুয়ার বেশী জলদকে ভূপাতিত করে বলে ওঠেন- এই নাও ইংরাজ দুশমন ! এই নাও নারী ধর্ষক ইংরাজ হার্মাদ। আজ বছরের পর বছর আমার দেশরে যা দিয়েছো, এই নাও তার খানিক ফেরৎ নাও!’ দর্শকদের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে যদু গাইতে শুরু করেন মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা’ নাটকের প্রস্তাবনা অংশের গান— ‘শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি’। পুলিশ কমিশনার ল্যামবার্টের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অভিনেতাদের সমবেতভাবে এই গানটির মধ্যে দিয়েই নাটকটি শেষ হয়।
প্রথম দৃশ্য থেকেই ধাপে ধাপে যে উত্তেজনা নাটককার তৈরি করছিলেন এই সপ্তম তথা শেষ দৃশ্যে এসে তা পরিণতি প্রাপ্ত হল। আমরা এই দৃশ্যটিকে Conclusion বা Denouement বলে অভিহিত করতে পারি। বেণীমাধব যে রকমের নাটক করছিলেন, তার বিরুদ্ধে সমাজের নিচের তলার মানুষ মেথর মথুর তাঁকে প্রথম আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। পরে প্রিয়নাথ মল্লিকও তাকে বলেছিলেন, ‘বাইরে পূরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে, আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করছেন!’ নাটক যত এগিয়েছে আমরা বেণীমাধবের ভিতরে যে দ্বিধা-দন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা চলছে তা ক্রমশ বুঝতে পেরেছি। প্রিয়নাথের লেখা ব্রিটিশ বিরোধী নাটক ‘তিতুমীর’ শেষ মুহুর্তে বাতিল করলেও সেই নাটকের সংলাপ তাঁর রক্তের মধ্যে প্রতিবাদের বীজ বপন করে দিয়েছিল। সহযোদ্ধা নাট্যকর্মীদের নাটক করার অপরাধে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তিনি ভিতরে ভিতরে অবশ্যই ব্যথিত হয়েছিলেন। ইংরেজ বেনিয়ার পা-চাটা বাবুদের প্রতি তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণা তিনি ‘সধবার একাদশী’ নাটকের সংলাপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করছিলেন তাদের প্রতিনিধি বীরকৃষ্ণ দাঁ কে লক্ষ্য করে। তারপর সামনে পুলিশ কমিশনার ল্যামবার্ট ও তার সঙ্গীদের দেখে তাঁর মনের গভীরের জ্বালা ও ক্ষোভ তিনি উগরে দেন রক্তের ভিতরে ঢুকে যাওয়া তিতুমীরের জ্বলন্ত সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এভাবেই একজন নাট্যকর্মী হিসেবে পরাধীন ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন টিনের তলোয়ার হাতে নিয়ে।
১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট উৎপল দত্তের নির্দেশনায় পি.এল.টি. নাট্যদল রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এই নাটকটি প্রথম অভিনয় করে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এ নাটকটি একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ নাটকের আলোক পরিকল্পনায় ছিলেন তাপস সেন, মঞ্চসজ্জায় মনু দত্ত, সঙ্গীত পরিচালনায় প্রশান্ত ভট্টাচার্য। নির্দেশনার পাশাপাশি এ নাটকের অন্যতম চরিত্র দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার নির্দেশক বেণীমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবু চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। উৎপল দত্ত। বাংলা নাট্যশালার আদিযুগে যে সমস্ত নাট্যশিল্পীরা একদিকে ইংরেজ সরকারের রক্তচক্ষু আর অন্যদিকে গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ভ্রকুটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাংলা নাটকের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলা পেশাদারী নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তিতে তাই সেইসব মহান মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করলেন উৎপল দত্ত তাঁর এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের ভূমিকায় তাই তিনি লিখেছিলেন – “বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে – যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়-বেদনাকে দিয়েছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি। ……….. যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া, বাঁধনহারা। যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ। যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র। যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী।২
এ নাটকের অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা সেইসময় অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন- শোভা সেন (বসুন্ধরা), সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (কামিনী), সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (হরবল্লভ), শান্তিগোপাল মুখোপাধ্যায় (জলদ), শ্যামল ভট্টাচার্য (যদুগোপাল), আশু সাহা (নটবর), সমীর মজুমদার (বীরকৃষ্ণ দাঁ), ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (ময়না), মুকুল ঘোষ (মেথর), অসিত বসু (প্রিয়নাথ), চিত্ত দে (বাচস্পতি), মন্টু ব্রহ্ম (গুন্ডা), কনক মৈত্র (মুদি) প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। এই নাটক সেইসময় বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। এ নাটক সেইসময় এতটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষের কাছে যে, উৎপল দত্তের মুচলেকা কান্ড ঘিরে যে অপপ্রচার হয়েছিল সর্বস্তরে সেই হৃত সম্মান তিনি আবার ফিরে পেয়েছিলেন এই নাটকের পর থেকে। প্রায় নয়মাস ধরে এক নাগাড়ে এই নাটকের মহলা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল আরও দুটি নাটক ‘ঠিকানা’ এবং ‘সূর্যশিকার”।
এই তিনটে নাটক নিয়ে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পি.এল.টি. উৎপল দত্তের নেতৃত্বে শুরু করে তাঁদের জয়যাত্রা। তবে জনপ্রিয়তায় ‘টিনের তলোয়ার’-এর কাছে বাকি নাটক দুটি কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের বাবু সমাজ, থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নাট্যপরিচালকদের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্ক, তাঁদের জীবন-যন্ত্রণা, সেকালের অভিনেত্রীদের যে বহুরকমের অসুবিধে ও আপোষের মধ্যে দিয়ে যেতে হত এই সমস্ত কিছুই খুব প্রাঞ্জলভাবে উৎপল দত্ত ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। এমনকি এইসব বাণিজ্যিক থিয়েটার গুলির মালিকের সঙ্গে সেই দলের নাট্যপরিচালক ও অভিনেত্ববর্গের কেমন সম্পর্ক ছিল তা-ও পরিস্ফুট হয়েছে এই নাটকে। এই নাটকটি উৎপল দত্ত রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহের কথা, সেই মঞ্চের রিভলভিং স্টেজের কথা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করেছিলেন। কারণ তখন তো আর তাঁর হাতে মিনার্ভার মতন কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। ঠিকানা বা ‘সূর্যশিকার’ নাটকটি অন্য মঞ্চে করা সম্ভব হলেও ‘টিনের তলোয়ার নাটকটির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসদনের ঘূর্নায়মান মঞ্চের সুবিধেটুকু ব্যবহারের কথা মাথায় নিয়েই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কারণ এ নাটকে নাটকের মধ্যে আর এক নাটক অভিনীত হতে দেখি আমরা। যে সময়ে নাটক ও তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ দেখে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে এক কালা কানুন প্রবর্তন করে থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করার জন্য, ১৮৭৬ সালের সেই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এ নাটক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আপাত নিরীহ এ নাটকটিকেও ‘অশ্লীল’ তকমা দিয়ে, রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে এর অভিনয় বন্ধ করে দেয় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর কংগ্রেস সরকার ১৯৭২ সালের ১ জুলাই। এবং সে কাজে তাঁরা ঐ ১৮৭৬ সালে তৈরি হওয়া ইংরেজদের কালা কানুনটিকেই ব্যবহার করেছিলেন এ নাটক সরকারি মঞ্চ রবীন্দ্রসদনে না হতে দেওয়ার জন্য। তবুও এ নাটক কে বন্ধ করা যায় নি। কলামন্দির বা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চ ভাড়া করে উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের উপস্থাপনায় সামান্য বদল করে নিয়ে এ নাটকটিকে চালিয়ে গেলেন অতি সফলভাবে। এই নাটকটি ছিল একইসঙ্গে থিয়েটার এবং বাংলা নাটকের এক ইতিহাস। ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ রায় তাই এ নাটক সম্পর্কে বলেছিলেন – “তুমি টিনের তলোয়ার’ দেখেছ ? ওই হল ভারতীয় থিয়েটারের হাইট ………. আমি তো কখনই উৎপলের Great massive নাটকের শো গুলি করতে পারতাম না। উৎপলের কয়েকটি থিয়েটার দেখা আমার কাছে phenomenal experience.৩
সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন “পিপলস লিটল থিয়েটারের টিনের তলোয়ার’ এক অপূর্ব নাট্যসৃষ্টি । ব্যক্তিগতভাবে একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আমি দীর্ঘকাল এমন আশ্চর্য নাটক এবং অসামান্য অভিনয় দেখি নি। উৎপল দত্ত যে একজন কতবড় শিল্পী এবং কতবড় শিল্পস্রষ্টা, ‘টিনের তলোয়ার” তার নতুনতম প্রমাণ। সেদিন রবীন্দ্রসদনে এই নাটক দেখে আমার মত প্রায় সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন এবং সেদিন প্রেক্ষাগৃহে যে সমস্ত গুণী ও সমঝদার দর্শকের সমাগম হয়েছিল, তাঁরা অভিনয় চলাকালেও নিজেদের আনন্দোপল্পব্ধি গোপন করতে পারেন নি। সমগ্র আবহাওয়া এমনভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।………. সমগ্র উনবিংশ শতকের সামাজিক জীবনের মুৎসুদ্দি-বেনিয়া চিত্রটা এমন অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছিল যে, সেটা বুঝবার জন্য বোধহয় ইতিহাসের পাতা ওল্টাবার দরকার ছিল না – যদিও একথা সত্য যে, সেই ইতিহাস যাঁদের জানা ছিল, তাঁদের কাছে ‘টিনের তলোয়ার’-এর মর্মভেদী বিদ্রুপ, শ্লেষ ও বাক্যবাণ যত ইস্পাতের তলোয়ারের মত তীব্র আঘাত হানছিল ! অনেকদিন রঙ্গমঞ্চে এমন সামাজিক কষাঘাত দেখিনি। ……….. টিনের তলোয়ার’-এর অভিনয়ের কোনো তুলনা নেই। প্রকাশভঙ্গীর সূক্ষ্ম-বাক্যের উচ্চারণে ও সংলাপের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনায় এবং অভিনয়-কলার নিখুঁত পারদর্শিতায় এই বই একেবারে জমজমাট। উৎপল দত্তের নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বলতম সাক্ষর ‘টিনের তলোয়ার।”৪
টিনের তলোয়ারের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রবল জনমতের দাবিতে চাপে পড়ে কংগ্রেস সরকার পরে আবারও পি. এল.টি. কে রবীন্দ্রসদনে অভিনয় করতে দিতে বাধ্য হয়। উৎপল দত্তের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার’ গ্রন্থে এ নাটক সম্বন্ধে লিখেছিলেন – “বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এমন কতগুলি নাটক আছে যা যুগান্তকারী হিসেবে গণ্য হয়েছে, “টিনের তলোয়ার’ সেই অর্থে ‘নীলদর্পণ’, ‘প্রফুল্ল’, ‘নবান্ন’ প্রভৃতির সঙ্গে একনিশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য নয় বরং একইসঙ্গে তার প্রয়োগ- নৈপুণ্যের জন্যও বটে।……….. টিনের তলোয়ার তৎকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জীবনের টানাপোড়েন, পরিবর্তনের স্রোত, সেই উত্তাল সময়ের থিয়েটারের আপোসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকাকে সুষম শিল্প হিসেবে হাজির করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেছে।”৫
১৮৭৬ সালের কলকাতার পেশাদারি থিয়েটার ছিল এ নাটকের পটভূমি। যে সময় ইংরেজ শাসক বাংলা থিয়েটারের বিপ্লবী আচরণে ভীত হয়ে নাট্যশালায় পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সে বছরের ১৬ ডিসেম্বর এক নতুন বিল তৈরি করেন। এই নাটক সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছে খুবই নিপুণভাবে তার একাধিক স্তর সমেত। এবং সে কালের নাট্যশিল্পীদের লড়াইয়ের কথা তুলে এনে এ কালের থিয়েটারকর্মীদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ তাঁরাই আজ সেই বাংলা নাট্যশালার ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলবেন ভবিষ্যতের দিকে। তাই শাসকপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, কারাগারে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত না হয়ে নাটকের শেষ দৃশ্যে কাপ্তেনবাবু নিমচাঁদের সংলাপ বলতে গিয়ে বলে ওঠেন তিতুমীরের সংলাপ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ল্যাম্বার্টসাহেবের সম্মুখে। বেণীমাধব ওরফে কাপ্তেনবাবুর থিয়েটার আপোষের থিয়েটার থেকে উন্নীত হয় বিপ্লবী থিয়েটারে। সে পুলিশের বড়কর্তাদের সামনে টিনের তলোয়ার তুলে ধরে তাদের শাসানিকে উপেক্ষা করে।
উৎপল দত্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিনের তলোয়ার’ নাটক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন। “First of all we rehearsed for nine months……… – ওটা যেহেতু পি.এল.টি.-র প্রথম বড় production সেহেতু আমরা অনেক সময় নিলাম।…… ‘টিনের তলোয়ার’-এ মনে হচ্ছিল, everybody was enjoying himself………..তাছাড়া সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে জানছে বুঝছে। নতুন একদল ছেলে মেয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, পরস্পরের অভিনয় technique-এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তারও একটা আনন্দ। সব মিলে, জিনিসটা হল। মোটামুটি ভালোই হল।……….আমার মনে হয় যে ‘টিনের তলোয়ার’-এর যে বক্তব্য সেটা তো থিয়েটারের বক্তব্য। থিয়েটার যেন বলছে পৃথিবীকে……….এই বক্তব্যের সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একমত হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ওরাও নিজেদের বক্তব্যটা বলতে পারে এই নাটকের মধ্যে দিয়ে। তাই বোধহয় team work এবং অভিনেতাদের আন্তরিকতা এত পরিস্ফুট হয়েছিল।’৬
পি.এল.টি নাট্যদল হিসেবে তিনটে নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে। ‘ঠিকানা”, “টিনের তলোয়ার’ এবং ‘সূর্যশিকার’, এই তিনটে নাটক কে যথাযথভাবে প্রস্তুতির জন্য তাঁরা দীর্ঘদিন মহড়া দিয়ে নিজেদের কে সেইভাবে তৈরি করেছিলেন উৎপল দত্তের নেতৃত্বে। কারণ এল.টি.জি. দল থেকে কয়েকজন পুরোনো সহযোদ্ধা ছাড়া এই পি.এল.টি. তে অনেক নতুন শিল্পীরা এসে উৎপল দত্তের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সেইজন্যই বেশ কিছুটা সময় লেগে যায় প্রস্তুতির, এবং তার ফল তো আমরা দেখতেই পাই যে কিভাবে আবারও এল.টি.জি.-র মতই পি.এল.টি. নাট্যদল তাদের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা এবং টিম ওয়ার্ক দেখিয়ে মানুষের মন জয় করে নেয়। ঐতিহাসিক ড. সুমিত সরকার ২০০৫ সালে উৎপল দত্ত স্মারকবক্তৃতায় উৎপল দত্তের নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ’ শীর্ষক আলোচনায় বলেছিলেন যে, “অনেক ঐতিহাসিকের চেয়ে উৎপলবাবু ইতিহাস ভালো বুঝতেন। নাটকগুলো পড়ে আমার মনে হয়। ………..অতীত সম্পর্কে লিখতে গেলে বা কল্পনা করতে গেলে সেই যুগ সম্পর্কে একটা সহানুভূতি বা empathy থাকা দরকার। empathy-র সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় একটা distance দরকার, ……….মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে বিভিন্ন স্তর এটার চমৎকার একটা ছবি ‘টিনের তলোয়ার’-এ আমরা পাই।………..টিনের তলোয়ার’ যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তার কারণ হচ্ছে একটা distance empathy ” ৭
ইতিহাস ছিল উৎপল দত্তের অন্যতম প্রিয় বিষয়। তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক পটভুমিকায় লেখা নাটকে সেই যুগ, সেই সময়ের একটা সমগ্র সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার নানা স্তর নিয়ে। এই ‘টিনের তলোয়ার নাটকের মধ্যেও আমরা সেদিনের বাংলা থিয়েটারের একটা সামগ্রিক চিত্রকে খুঁজে পাই। বসুন্ধরা, ময়না প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে সেকালের বহু অভিনেত্রীর জীবন যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও সামাজিক অবস্থান সব কিছুই ফুটে ওঠে। মুৎসুদ্দি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় থেকেও কিভাবে সেদিনের বাংলা থিয়েটার ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একের পর এক নাটকে গর্জে উঠেছিল বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সেই ঘটনার এক দলিল হয়ে ওঠে এ নাটক। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থই লিখেছেন।
“১৯৭১-এর আগস্ট মাসে যে তিনটি নাটক নিয়ে উৎপলবাবুর নতুন নাট্যগোষ্ঠী পীপলস লিটল থিয়েটারের কর্মারম্ভ, তার মধ্যে ‘টিনের তলোয়ার একেবারেই স্বতন্ত্র। থিয়েটারের মধ্যে নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্পর্ক, নাটকের সঙ্গে প্রযোজনা পরিবেশনার সম্পর্ক, থিয়েটারের বাইরে থিয়েটারের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক, থিয়েটারের সঙ্গে সমকালীন বাস্তব ও বিশেষত রাজনীতির সম্পর্ক এই চারটি সম্পর্ক ধরে নাট্যকার এগিয়েছেন থিয়েটারের অস্তিত্বেরই – বিশ্লেষণে। থিয়েটারের অস্তিত্বের যে সংগ্রাম তাতে সৃষ্টির স্ফূর্তিও ব্যবসায়িক বেচাকেনার হিসেব। অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত সাধ-আহ্লাদ আদর্শ ও পরিচালকের কল্পনা ও সিদ্ধান্তের তার সবই বিসর্জন দেবার দায়। দর্শককে টানতে প্রমোদপকরণের সম্ভার সাজানো ও নাটককে যথার্থ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কাব্যের স্তরে উন্নীত করার প্রাণান্ত প্রয়াস, দেশের রাজনীতিতে অবস্থান গ্রহণ করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করার উচ্চাশা ও শাসককুল ও ধণীদের দাক্ষিন্য ও প্রশ্রয়ে সুস্থিত থাকায় লোভ, এই দ্বন্দ্বগুলি পেশাদার থিয়েটারের স্বভাবধর্মেই পরিণত হয়ে গেছে। উনিশ শতকের কলকাতায় ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের অবস্থান নানাভাবেই চিহ্নিত – হুতোমি ভাষা ও শহরের রাস্তার ভাষার সহাবস্থানেই শুধু নয়; হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবসাধেও ও তার ব্যর্থতাতেও বটে; আবার ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রন অর্ডিনানস-এর প্রয়োগেও। ইতিহাসে উপস্থিত গ্রেট ন্যাশনাল, অর্ধেন্দুশেখর, সুকুমারী দত্ত, উপেন দাস, সধবার একাদশী’ নাটকাভিনয় যেমন প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষ উল্লেখে এই নাটকে স্থান করে নিয়েছে, তার পাশাপাশি কল্পনাপ্রসূত বেণীমাধব, বসুন্ধরা, ময়না, প্রিয়নাথ, কিংবা ‘ময়ূরবাহন’ ও ‘তিতুমীর’ নাটকের অভিনয় ইত্যাদির অবস্থানও যেন ওই ঐতিহাসিক নাম-ঘটনাগুলির সান্নিধ্যে ও যোগে ঐতিহাসিক বাস্তবের চারিত্র্য পেয়ে যায়। ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিককে মেলাবার এই কারিগরি যেন ইতিহাসে অলক্ষিত বা অলিখিত কিছু সম্ভাব্য সত্যকে স্পর্শ করবার সুযোগ এনে দেয় যেমন সুযোগ সৃষ্টি হয় বসুন্ধরার – চেতনায় পেশাদারি থিয়েটারে বা থিয়েটারি ব্যবসায় অভিনেত্রীর স্থান ও মর্যাদা বিষয়ে ক্ষোভের প্রথম সঞ্চারের।”৮
অর্থাৎ যে সামগ্রিকতার কথা আমরা বলছিলাম সেই সামগ্রিকতা তার সমস্ত স্তর সমেত ঊনবিংশ শতক থেকে উঠে আসে এ নাটকে। তৈরি হয় একটি যুগের যথাযথ চিত্র। প্রতিটি চরিত্র তার অন্তর্দ্বন্দ্ব্ব, বিশেষ করে বসুন্ধরা ও ময়না চরিত্র দুটির ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই প্রাঞ্জলভাবে ফুটে উঠতে দেখি এ নাটকে। ময়না-র মধ্যে বিনোদিনীর ছায়া ফুটে ওঠে, বেণীমাধবের মধ্যেও কি গিরিশ ঘোষ কে খুঁজে পাই না আমরা ? এভাবেই পুরো ১৮৭৬ সালের বাংলা নাট্যশালা হাজির হয় আমাদের সামনে তার পুরো যুগচিত্রটি নিয়ে।
তথ্যসূত্র
১। দত্ত, উৎপল। ‘আশার ছলনে ভুলি’, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৩, পৃ – ৯।
২। দত্ত, উৎপল। ‘টিনের তলোয়ার নাটকের উৎসর্গ পত্র’, নাটক সমগ্র ৫ম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ – ৭৩।
৩। রায়, সত্যজিৎ। অরুপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এপিক থিয়েটার, সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে শোভা সেন, মার্চ ২০০৭, পৃ – ৬৪।
৪। মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ। ‘টিনের তলোয়ার’, এপিক থিয়েটার, সম্পাদক – উৎপল দত্ত, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ- ২৪-২৫।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য। উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটার‘, প্যাপিরাস, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৬, পৃ-৮৯-৯০ ৬। দত্ত, উৎপল। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, শূদ্রক, সম্পাদক – দেবাশিস মজুমদার, শরৎ ১৪০০, পৃ – ১৪১-১৪২।
৭। সরকার, ড. সুমিত। উৎপল দত্তের নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ‘, এপিক থিয়েটার, সম্পাদকম্পন্ডলীর পক্ষে শোভা সেন, আগস্ট ২০০৫, পৃ – ১২-১৩।
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক। ভূমিকা, নাটক সমগ্র ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ – ৭।বি. দ্র. এই প্রবন্ধে উল্লেখিত ‘টিনের তলোয়ার‘ নাটকের সমস্ত উদ্ধৃতি উৎপল দত্তের নাটক সমগ্র ৫ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭ থেকে গৃহীত হয়েছে।